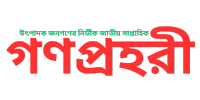কায়সার রহমান রোমেল :মুই হনু কামলা পাই ভাত এক গামলা। উত্তরের জেলা গাইবান্ধার কৃষি প্রধান অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো কৃষিশ্রমিক। ইতিহাস বলছে ১৩৯ বছরেও শ্রমিকদের মে দিবসের দাবী বাস্তবায়িত হয়নি এদেশে। সেক্ষেত্রে কৃষি শ্রমিকের মজুরি নিয়েতো কেউ জীবন দেননি, আন্দোলন হয়নি। কৃষকরা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। অথচ মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। সে কারণেই কৃষকদের আক্ষেপ হচ্ছে- ‘মুই হনু কামলা, সারাদিন কাম দিলে, ভাত এক গামলা’ এটি কৃষিপ্রধান এ অঞ্চলের একটি প্রচলিত আঞ্চলিক প্রবাদ। এখানকার কৃষিশ্রমিকদের শ্রমে-ঘামেই এ অঞ্চলের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠের পর মাঠ তারা ফসল ফলানো, পরিচর্যা এবং সোনা রাঙা ফসল ঘরে তোলার কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। রোদ-বৃষ্টি কিংবা শীত উপেক্ষা করে তাঁদের শ্রম কৃষি উৎপাদনের চাকাকে সচল রাখে। এই বিপুল শ্রমের বিনিময়ে কৃষিশ্রমিকরা যে মজুরি পান, তা তাঁদের জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট নয়। অন্যদিকে কৃষিপ্রধান এ অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে নারী কৃষিশ্রমিকদের অবদান। বীজ বপন থেকে শুরু করে ফসল তোলা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে তাদের শ্রমও ফসল উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা রাখে। অথচ পুরুষের সমান তালে কাজ করেও নারী কৃষিশ্রমিকরা প্রায়শই ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হন।
মহান মে দিবস, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের এক ঐতিহাসিক দিন। দীর্ঘ সংগ্রাম আর আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই দিনটি শুধু শ্রমিক শ্রেণির ঐক্য ও সংহতির প্রতীকই নয়, একইসাথে বিশ্বের সকল শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারের দিন। প্রতি বছর এই দিনে শিল্প কারখানার শ্রমিকদের অধিকারের কথা বিশেষভাবে উচ্চারিত হলেও, কৃষি প্রধান অর্থনীতির অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই কৃষিশ্রমিকরা আলোচনার বাইরে থেকে যায়।
বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং সমাজের বিশিষ্টজনরা বলছেন, মহান মে দিবসের তাৎপর্য তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন আমরা সকল শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের কথা বলবো। কৃষিশ্রমিকরা আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তাদের ন্যায্য মজুরি, কর্মঘণ্টার নির্দিষ্টতা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং শ্রমিকবান্ধব নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব। সরকার, কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, বেসরকারি সংস্থা এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া কৃষিশ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গাইবান্ধা সূত্রে জানা যায়, ২ হাজার ১৪৩ দশমিক ২৯ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের গাইবান্ধা জেলার ৭টি উপজেলায় ৪টি পৌরসভা এবং ৮২টি ইউনিয়নে গ্রাম রয়েছে ১ হাজার ২৫৫টি। এখানকার জনসংখ্যা ২৪ লাখ ৫৫ হাজার ৭১৯ জন। এরমধ্যে শতকরা ৫৪ ভাগ পুরুষ এবং ৪৬ ভাগ নারী। জেলা জুড়ে মোট পরিবারের সংখ্যা ৬ লাখ ১১ হাজার ২৮৩টি। এরমধ্যে শতকরা ৯৮ ভাগই কৃষি পরিবার। জেলার ৬ লাখ ১ হাজার ৭২১টি কৃষক পরিবারের মধ্যে শতকরা ৩৮ ভাগই প্রান্তিক কৃষক পরিবার, ৩১ ভাগ ক্ষুদ্র কৃষক, ২০ ভাগ ভূমিহীন কৃষক, ৯ ভাগ মাঝারি কৃষক এবং মাত্র ২ ভাগ বড় কৃষক পরিবার রয়েছে। জেলায় মোট কৃষি পরিবারের মধ্যে বর্গা চাষি পরিবারের সংখ্যা ৭১ হাজার ৭৭২টি। জেলার সাত উপজেলাজুড়ে কৃষি বিভাগের তালিকাভুক্ত ৫৫ হাজার ৬৫০ জন কৃষিশ্রমিক রয়েছে।
জেলার গ্রামীণ জনপদে সরেজমিনে ঘুরে দেখা যায়, কৃষিশ্রমিকরা সাধারণত দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করেন। বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি কাজের ধরন ও মওসুমের ওপর ভিত্তি করে এই মজুরির কিছুটা তারতম্য দেখা যায়। তবে সাধারণভাবে, তাদের দৈনিক মজুরি অন্যান্য অনেক পেশার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির এই সময়ে, স্বল্প মজুরি তাদের পরিবারকে দারিদ্র্য সীমার নিচেই রেখে দেয়।
অপরদিকে একই ধরনের কৃষি কাজে নিয়োজিত পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় নারী শ্রমিকরা কম মজুরি পান। ধান রোপণ, আগাছা পরিষ্কার, ফসল কাটা কিংবা বোঝা টানার মতো পরিশ্রমসাধ্য কাজেও এই বৈষম্য সুস্পষ্ট। অনেক ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ বা তারও কম হয়ে থাকে। এই বৈষম্য শুধু আর্থিক কষ্টের কারণ নয়, এটি নারী শ্রমিকদের সামাজিক মর্যাদা এবং ক্ষমতায়নের পথেও একটি বড় বাধা।
গাইবান্ধা মূলত একটি কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এখানকার অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো কৃষি এবং এই কৃষিকে সচল রাখেন কৃষিশ্রমিক। অথচ তাঁদের জীবনযাত্রার মান, শ্রমের মর্যাদা এবং অধিকার আজও বহুলাংশে উপেক্ষিত। শিল্প শ্রমিকদের জন্য যেমন নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা, ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারের মতো বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি কৃষিশ্রমিকদের জন্যও এসব অধিকার অপরিহার্য। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ কৃষিশ্রমিক আজও দৈনিক ভিত্তিতে কাজ করেন, যাঁদের কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। ফসলের মওসুমের উপর নির্ভর করে তাদের আয় অনিশ্চিত থাকে। নেই কোনো নিয়োগপত্র, নেই স্বাস্থ্যসেবা বা সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি আরও বাড়ায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি ঘটলে তাদের কষ্টের সীমা থাকে না।
কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়লেও, এখনও অনেক কাজ শ্রমিকনির্ভর। বীজ বপন থেকে শুরু করে ধান কাটা, মাড়াই করা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে কৃষিশ্রমিকের অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। তারা জমিতে সার দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার এবং ফসলের রোগ প্রতিরোধের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোও করে থাকেন। এত কঠিন এবং শারীরিক শ্রমনির্ভর কাজ করার পরেও তাদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্যিই হতাশাজনক।
কৃষিশ্রমিকদের কম মজুরির পেছনে বেশ কিছু কারণ বিদ্যমান। এর মধ্যে অন্যতম হলো মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য। অনেক ক্ষেত্রে কৃষিপণ্য বিক্রি এবং শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীরা একটি বড় ভূমিকা পালন করে। ফলে কৃষকের কাছ থেকে কম দামে ফসল কিনে এবং শ্রমিকদের কম মজুরি দিয়ে তারা নিজেরাই লাভবান হয়। এছাড়া, কৃষকদের আর্থিক অসচ্ছলতা এবং দর কষাকষির অভাবের কারণেও শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হন।
কৃষিশ্রমিকদের এই দুরবস্থা দেশের কৃষি খাতের ভবিষ্যতের জন্য একটি অশনি সংকেত। যদি এই শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি এবং সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা না যায়, তবে ভবিষ্যতে কৃষিকাজে আগ্রহ কমে যেতে পারে। এর ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
অন্যদিকে, নারী কৃষিশ্রমিকদের মজুরি বৈষম্যের পেছনেও একাধিক কারণ বিদ্যমান। প্রথমত, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে নারীরা পুরুষের মতো শারীরিক শ্রম দিতে সক্ষম নন অথবা তাদের কাজের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম। এই ধারণা প্রচলিত থাকার কারণে নিয়োগকর্তারা নারীদের কম মজুরি দিতে দ্বিধা বোধ করেন না। দ্বিতীয়ত, নারী শ্রমিকদের দর কষাকষি করার ক্ষমতা কম থাকে। পারিবারিক ও সামাজিক চাপের কারণে অনেক নারী শ্রমিক কম মজুরিতেও কাজ করতে বাধ্য হন। এছাড়া, সংগঠিত শ্রমিক সংগঠনের অভাব এবং আইনি সুরক্ষার দুর্বলতাও এই বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। তৃতীয়ত, কিছু ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকরা দৈনিক মজুরির পরিবর্তে চুক্তিভিত্তিক বা ফসলের একটি অংশের বিনিময়ে কাজ করেন, যেখানে তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক পাওয়ার সুযোগ আরও সীমিত হয়ে যায়।
মজুরি বৈষম্যের কারণে নারী কৃষিশ্রমিকরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। তাদের সীমিত আয় পরিবারের ভরণপোষণ, সন্তানদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার জন্য যথেষ্ট হয় না। ফলে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েন তারা। এছাড়াও, ন্যায্য মজুরি না পাওয়ার কারণে অনেক নারী শ্রমিক কৃষি কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন এবং জীবিকার সন্ধানে অন্য পেশায় যেতে বাধ্য হন, যা কৃষি উৎপাদনকেও প্রভাবিত করতে পারে।
কৃষিশ্রমিকদের মজুরি বৈষম্য দূরীকরণে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন উল্লেখ কওে জাতীয় কৃষক-ক্ষেতমজুর সমিতির জেলা সভাপতি ও কৃষক-ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদের জেলা সমন্বয়ক রেবতী বর্মন বলেন, কৃষিশ্রমিকদের জন্য একটি ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কঠোর নজরদারি রাখা উচিত। সেইসাথে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমানোর জন্য সরাসরি কৃষক এবং শ্রমিকদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়াও কৃষিশ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত। তিনি বলেন, কৃষিশ্রমিকরা আমাদের অর্থনীতির মেরুদ-। তাদের শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন, ন্যায্য মজুরি এবং জীবনমানের উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমেই আমরা একটি সমৃদ্ধ ও টেকসই কৃষি খাত গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।
বাাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আহসানুল হাবীব সাঈদ নারী কৃষিশ্রমিকদের মজুরি বৈষম্য প্রসঙ্গে বলেন, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারীর কাজের প্রতি সম্মান জানানোর মানসিকতা তৈরি করতে হবে। গণমাধ্যম এবং শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে লিঙ্গবৈষম্যমূলক ধারণাগুলো পরিবর্তন করতে হবে। সেইসাথে নারী কৃষিশ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার এবং তাদের অধিকার আদায়ের জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে। শ্রমিক ইউনিয়ন এবং নারী অধিকার সংগঠনগুলো এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি বলেন, মজুরি বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা কেবল মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই জরুরি নয় বরং একটি টেকসই কৃষি ব্যবস্থার জন্যও অপরিহার্য। সরকার, বেসরকারি সংস্থা এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই বৈষম্য দূর করতে এবং নারী কৃষিশ্রমিকদের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করতে পারে।
আরও পড়ুন – স্মার্ট প্রকল্পের স্মার্ট দুর্নীতি : বঞ্চিত শুধু কৃষক
মুই হনু কামলা, মুই হনু কামলা