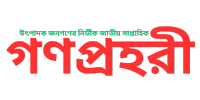ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
রাষ্ট্রের ওঠানামা-অতীতে বাঙালির চিন্তায় অর্থনীতি যে উপযুক্ত গুরুত্ব পায়নি বাঙালির পক্ষে তা গৌরবের বিষয়গুলোর একটি নয়। মোটেই না। যেমন ধরা যাক, ইংরেজ শাসনের ব্যপারটা। দালাল কিসিমের লোকেরা বলত, ইংরেজ আমাদেরকে ভাষা, সভ্যতা-ভব্যতা, সংষ্কৃতি ওসব অনেক কিছুই শিখিয়েছে। যারা অতটা ইংরেজভক্ত নন তাঁরাও বলেন, ইংরেজের সংস্পর্শে আসার কারণেই উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার একটি রেনেসান্স ঘটে গেছে। এ একটা অতিকথন মাত্র। রেনেসান্স বলতে ইউরোপে যা ঘটেছিল বাংলার তেমন কিছু ঘটেনি; তবে হ্যাঁ, বিশ্বজয়ে অভিপ্রায়ী ইউরোপের প্রতিনিধি ইংরেজদের সঙ্গে যোগযোগের ফলে অনেক ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। কিন্তু এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত জরুরি যে বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয় তা হলো অর্থনৈতিকভাবে বাংলা নিঃস্বকরণ। ব্যবসা-বানিজ্য, প্রশাসন ইত্যাদির নামে শোষণ তা ছিলই, সেই সঙ্গে ঘটছিল সম্পদ পাচার, পুঁজির বিকাশকে অসম্ভব করে তোলা এবং দেশীয় শিল্পকে বিনষ্ট করে দেয়া। ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক ছিল লাভের তুলনায়।
রাষ্ট্রের ওঠানামা
যাঁরা রেনেসান্স ঘটেছে বলে দাবি করছিলেন তাঁরা এটাও খেয়াল করেননি যে বাঙালি সংষ্কৃতিতে সেদিন যাঁরা গৌরবজনক অবদান রাখছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের জন্য একটি অর্থনৈতিক ভিত গড়ে নিয়েছিলেন, তাইতো রামমোহন রায় তাঁর কাজগুলো করতে পারলেন। মাত্র সাতাশ বছর বয়সে বিদ্যাসাগর যে সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিতে সাহস করেছিলেন সেটা দরকার হলে আলু-পটলের ব্যবসায় করেও খেতে পারবেন এই আত্মবিশ্বাস ছিল বলেই। অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্র যে ইংরেজকে শত্রু হিসেবে জেনেও উপন্যাসে তাকে সেভাবে চিত্রিত করতে সাহসী হলেন না সে জন্য অনেকাংশে তার সরকারি চাকরি-নির্ভরতাই যে দায়ী তাতে সন্দেহ করবার কারণ নেই।
রাষ্ট্রের ওঠানামা
ইউরোপে যে রেনেসান্সের ঘটনা ঘটেছিল সেটি ছিল পুরোপুরি ইহজাগতিক। তাতে ধর্ম ও জগতের মধ্যে একটি পারস্পারিক-বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা হয়েছিল। ধর্ম থাকবে ধর্মের জায়গায়, জগৎ জগতের স্থানে-এই ছিল বিধান। এর ফলে অর্থনৈতিক বিকাশ, যেমন পুঁজির সঞ্চায়ন, সামন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ধনতন্ত্রের দিকে অগ্রগমন, জাতীয়তাবাদ ও বাজার সৃষ্টি, সুগম হয়েছিল। বিদ্যার যে নবজাগরণ ঘটল তখন তার সামনে আদর্শ ছিল প্রাচীন গ্রীস, সেই গ্রীসের সংষ্কৃতি তার সমৃদ্ধ তার সমৃদ্ধ অর্থনীতির শক্তির ভিত্তির ওপরই গড়ে উঠেছিল। গ্রীক দার্শনিকরা ভোজনের ব্যাপারটাকে অবজ্ঞা করতেন না এবং তাঁদের গৃহে দাসদাসী থাকত। শূণ্য উদর নিয়ে যে দার্শনিক চিন্তা সম্ভব নয় সেটা না জানলে তারা দার্শনিক হতেন না; পেটে পাথ বেঁধে কায়িক শ্রম সম্ভব হলেও হতে পারে সুস্থ দার্শনিক চিন্তা যে একেবারেই অসম্ভব, এ তাঁরা জানতেন। অর্থনীতির এই ব্যাপারটাকে আমরা বাঙালিরা যে অবজ্ঞা করি সেটা আমাদের দার্শনিক দারিদ্র্যের প্রমাণও বটে, লক্ষণও বটে। আমাদের দেশে বামপন্থী আন্দোলনের একটা বড় দুর্বলতা ছিল এট যে, দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে বাস্তবাদী ধারণা বামপন্থীরা গড়ে তুলতে পারেননি, উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে তারা তর্ক করেছেন, কিন্তু যথার্থ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি।
রাষ্ট্রের ওঠানামা
যে যাই হোক, পূর্ববঙ্গকে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করতে হয়েছে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির প্রয়োজনেই। একদা পাকিস্তানের মানুষ সেই মুক্তি পাবে বলে আশা করেছিল যে জন্য তারা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। পরে যখন দেখল যে, পাকিস্তান সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে বরঞ্চ উল্টোটা করছে তখন তারা ই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভোট দিলো এবং যখন হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী যে পূর্ববঙ্গকে তাদের উপনিবেশ মনে করত, সে স্বাধীন হতে চাইছে দেখে গণহত্যা শুরু করল। বাঙালি তখন লড়াই করে তাদেরকে হটিয়ে দিলো। পাকিস্তানি শাসকদের জন্য মূল সমস্যাটা ছিল পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে। সত্তরের নির্বাচনের ‘পূর্ববঙ্গ শ্মশান কেন’ এ একটি পোস্টার বাঙালি ভোটারদের যেভাবে সচেতন করেছে তার মোকাবিলা করার মতো তথ্য বা বক্তব্য শাসকদের কাছে ছিল না। ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার, হিন্দু-মুসলিম বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা, স্থানীয়-অস্থানীয় প্রশ্নের উত্তেজনা তৈরি, উত্তরবঙ্গকে স্বতন্ত্র প্রদেশ স্থাপনের দাবিতে অনুুপ্রাণিত করা, ইসরামের নামে আহ্বান ইত্যাদির কোনোটিতেই কাজ হয়নি; লোকে বুঝে গেছে যে পাকিস্তানের অধীনে পূর্ববঙ্গ শ্মশানই রইবে, সোনার বাংলা হবে না। তাদের পক্ষে পাকিস্তানের পক্ষে থাকা কিছুতেই সম্ভব হলো না।
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যে কেবল পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি পাকিস্তানিরা দেবার পরও এ আন্দোলন শেষ হয়ে যায়নি। বরঞ্চ আরো এগিয়ে গিয়ে রূপ নিয়েছে উনসত্তরের গণঅভ্যূত্থানের এবং শেষ পর্যন্ত পরিণত হয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধে। অন্তরের আকাঙ্খাটা ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির। আর সে মুক্তি যে জিন্নাহ উল্লেখিত ওই পুঁজিবাদী পথে আসবে না সেই বোধটাও ছিল জনগণের মনে। ভাষা আন্দোলনের অর্থনৈতিক মুক্তির পথটাও বলে দিয়েছে। সেই পথটা হচ্ছে স্বাধীনতার। পূর্ববঙ্গকে স্বাধীন হতে হবে, কেননা স্বাধীন না হলে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে যতই সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়অ হোক না কেন অবাঙালিদের শোষণ শেষ হবে না। উদ্র্ইু থাকবে প্রধান, আর থাকবে অস্ত্র, থাকবে পুঁজির জোর, আমলাতন্ত্রের দাপট, সব মিলিয়ে পূর্ববঙ্গবাসী যাত্রী হবে শ্মশানের। স্বাধীনতার সঙ্গে ছিল মৈত্রীর বিষয়টিও। ভাষা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে, কাছে টেনে দাঁড় করিয়ে দেয়। সাদৃশ্য মুখ্য হয়ে ওঠে পার্থক্যের তুলনায়। তোমার ভাষাও বাংলা আমার ভাষাও বাংলা-পাকিস্তানী রাষ্ট্রকাঠামোতে বাঙালির জন্য ঐক্যের এ ছিল মূল সূত্র। জ্ঞাণের অন্বেষণে সংগৃহীত
[লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক, ইংরেজি বিভাগ]
আরও পড়ুন: স্বাধীনতা অর্জনে নেতৃত্বদানকারীদের যথাযথ মর্যাদাদান আবশ্যক