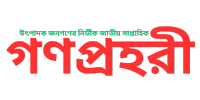সুদীপ্ত শামীম : গোপন নথি নয়, নাগরিকের শক্তি। তথ্য চাওয়াটা কি অপরাধ? আমাদের সমাজে আজও অনেকের কাছে এ প্রশ্নটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। নাগরিক, সাংবাদিক, গবেষক কিংবা শিক্ষার্থী—যখনই তারা সরকারি কোনো নথি, খরচের হিসাব, প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রমাণ বা সিদ্ধান্তের পেছনের যুক্তি জানতে চান—তখন যেন হঠাৎ করে সরকারি দপ্তরের মাথায় ঝড় ওঠে। কেউ বলে, ‘এগুলো গোপনীয়’; কেউ আবার নানা অজুহাত দাঁড় করিয়ে ফাইল ঘুরাতে থাকে; আবার কেউ সরাসরি বিরক্ত হয়ে বলেন, ‘তথ্য চেয়ে ঝামেলা করবেন না।’ যেন তথ্যের দাবি মানেই কর্তাদের অস্বস্তি, অস্থিরতা এবং মাথা নষ্ট হওয়ার উপক্রম। অথচ প্রকৃত সত্য হলো—তথ্য চাওয়া কোনো অপরাধ নয়, বরং এটি একটি মৌলিক অধিকার, যা রাষ্ট্র নিজেই আইন করে দিয়েছে।
তথ্য অধিকার দিবসের তাৎপর্য
প্রতি বছর ২৮ সেপ্টেম্বর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পালিত হয় আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। এই দিনটি মনে করিয়ে দেয়, জনগণের জানার অধিকারই গণতন্ত্রের প্রাণ এবং রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের আস্থার মূলভিত্তি। নাগরিকেরা যদি রাষ্ট্রের কাজকর্ম, বাজেট, প্রকল্প কিংবা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত না থাকে, তবে গণতন্ত্র কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তথ্য হলো সেই আলো, যা অন্ধকার দূর করে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।
২০০২ সালে লাতিন আমেরিকার এক সম্মেলনে প্রথমবার দিবসটি পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তারপর থেকে ধীরে ধীরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তথ্যের অধিকার আইনি স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। বর্তমানে প্রায় ১৩০টিরও বেশি দেশে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর রয়েছে। বাংলাদেশেও ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন হয় এবং ২০১০ সালের জুলাই থেকে তা কার্যকর হয়। আইনে স্পষ্টভাবে বলা আছে, যে কোনো নাগরিক সরকারি বা আধা-সরকারি দপ্তর থেকে তথ্য চাইতে পারবেন, আর তথ্য সরবরাহে গাফিলতি করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। কিন্তু বাস্তব চিত্র আশানুরূপ নয়। অধিকাংশ সরকারি দপ্তরেই এখনো তথ্যপ্রবাহ সহজ হয়নি। আবেদন করলে অনেক সময় নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য পাওয়া যায় না। কোথাও কোথাও অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দেওয়া হয়, আবার অনেকে সরাসরি জানিয়ে দেন, ‘এই তথ্য দেওয়া যাবে না।’ কর্মকর্তাদের মনে হয়, তথ্য প্রকাশ করলে তাঁদের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে বা তাঁরা দায়ে জড়িয়ে পড়বেন। এর ফলে নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার পরিবর্তে তৈরি হয় ভয়, অস্বস্তি আর কৃত্রিম গোপনীয়তা।
আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস তাই কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং আমাদের জন্য এক সতর্ক সংকেত—আইন থাকলেও যদি কার্যকর প্রয়োগ না হয়, তবে নাগরিক অধিকার অপূর্ণই থেকে যাবে। তথ্য চাওয়ার সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং তথ্য দেওয়াকে দায়িত্ব হিসেবে স্বাভাবিক করা—এই দুটি বিষয়কে এখনই গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার।
কেন তথ্য গুরুত্বপূর্ণ
তথ্য মানেই স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ন্যায়বিচারের চাবিকাঠি। গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও মানবাধিকার- নাগরিক সমাজের এই তিনটি মূল স্তম্ভের সঙ্গেই তথ্যের প্রবাহ অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। তথ্য এমন এক ভিত্তি, যার উপর দাঁড়িয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় নাগরিকের আস্থা গড়ে ওঠে এবং ক্ষমতাবানদের জবাবদিহি নিশ্চিত হয়।
দুর্নীতি দমন: সরকারি প্রকল্পে কত টাকা ব্যয় হলো, কতটা কাজ শেষ হলো, কিংবা কে টেন্ডার পেল—এসব তথ্য প্রকাশ না হলে দুর্নীতি ও অনিয়ম লুকিয়ে যায়। স্বচ্ছ তথ্যপ্রবাহ দুর্নীতিবাজদের জন্য ভয়ংকর বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, আর জনগণের করের অর্থ সঠিক জায়গায় ব্যয় হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করে।
জনগণের অংশগ্রহণ: গণতন্ত্র কেবল ভোটে সীমাবদ্ধ নয়; প্রকৃত গণতন্ত্র তখনই হয় যখন নাগরিকেরা রাষ্ট্রীয় নীতি ও পরিকল্পনায় মতামত দিতে পারে। কিন্তু তারা যদি বাজেট, প্রকল্প বা উন্নয়ন পরিকল্পনার তথ্যই না জানে, তবে অংশগ্রহণের সুযোগও থাকে না। তথ্য জানলেই তারা মতামত দিতে পারে, ভুল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে পারে।
গণমাধ্যমের স্বাধীনতা: সাংবাদিকদের দায়িত্ব সত্য প্রকাশ করা। কিন্তু সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ছাড়া সেই দায়িত্ব পূরণ সম্ভব নয়। সাংবাদিকরা যখন তথ্য পান, তখন তারা শুধু দুর্নীতি নয়, মানুষের উন্নয়ন, সাফল্য ও সমস্যাগুলোও তুলে ধরতে পারেন। ফলে সমাজে সচেতনতা বাড়ে, গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়।
অধিকার সংরক্ষণ: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জমি, পরিবেশ বা সামাজিক সুরক্ষা—এসব ক্ষেত্রেই তথ্য অপরিহার্য। কোথায় কী সুযোগ-সুবিধা আছে, কোন প্রকল্পে কত বরাদ্দ, কোথায় কী ভর্তুকি—এসব না জানলে সাধারণ মানুষ প্রতারিত হয় এবং প্রাপ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। তথ্য নাগরিককে তার অধিকার বুঝতে ও আদায় করতে সাহায্য করে।
উন্নয়নের গতি: উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় ও অর্থ কোথায় যাচ্ছে তা জনগণ জানলে কাজের গতি বাড়ে। তথ্যপ্রবাহ বাধ্য করে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকতে, ফলে প্রকল্প বিলম্ব বা অপচয় কমে যায়।
বিশ্বাস ও আস্থা: রাষ্ট্র যদি তথ্য গোপন করে, তবে জনগণের মনে সন্দেহ জন্মায়। আর তথ্য উন্মুক্ত হলে নাগরিক ও সরকারের মধ্যে আস্থা তৈরি হয়। এই আস্থাই একটি আধুনিক ও স্থিতিশীল সমাজের পূর্বশর্ত।
অতএব, তথ্য শুধু একটি প্রশাসনিক বিষয় নয়; এটি গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ, উন্নয়নের গতি এবং মানবাধিকারের গ্যারান্টি।
বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র
তথ্য অধিকার আইন কার্যকরের ১৫ বছর পেরিয়ে গেলেও বাংলাদেশে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন এখনো দৃশ্যমান নয়। বাস্তবতা হলো, ‘তথ্য চাইলে সরকারি কর্তাদের মাথা নষ্ট হয়’—এমন পরিস্থিতিই এখনো বহাল রয়েছে। সরকারি দপ্তরে তথ্য চাওয়াকে এখনো অনেকে ‘অসুবিধাজনক’ বা ‘বিরক্তিকর’ মনে করেন। ফলে নাগরিকরা তথ্যের অধিকার প্রয়োগ করতে গেলে নানা প্রতিবন্ধকতায় পড়েন।
আইন অনুযায়ী প্রতিটি দপ্তরে একজন তথ্য কর্মকর্তা থাকার কথা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হলেও তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পাননি। আবার অনেকেই জানেন না আইন অনুযায়ী তাদের করণীয় কী। তথ্য চাইলে ফাইল ঘুরতে থাকে টেবিল থেকে টেবিলে, দিন থেকে মাস কেটে যায়, অথচ কাঙ্ক্ষিত তথ্য নাগরিকের হাতে পৌঁছায় না।
তথ্য অধিকার আইনে স্পষ্ট বলা আছে, ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে মাসের পর মাস পেরিয়ে গেলেও অনেক সময় কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সময়ক্ষেপণ করেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়ে দায়সারা মনোভাব দেখানো হয়।
তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, প্রতিবছর হাজার হাজার অভিযোগ জমা পড়ে। এসব অভিযোগের বড় অংশই ঘুরপাক খায়—তথ্য না দেওয়া, তথ্য দিতে দেরি করা, বা অস্পষ্ট তথ্য দিয়ে নাগরিককে বিভ্রান্ত করা। এ ছাড়া তথ্য কমিশন নিজেও নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে। পর্যাপ্ত জনবল নেই, নেই পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা। ফলে অভিযোগের সঠিক নিষ্পত্তি সব সময় সম্ভব হয় না।
বাংলাদেশের অনেক সরকারি কর্মকর্তা এখনো তথ্য অধিকার আইনকে বোঝেন না বা বোঝার ভান করেন না। তাদের কাছে তথ্য প্রকাশ মানে নিজের কর্মকাণ্ডের হিসাব দিতে বাধ্য হওয়া। তাই তথ্যকে ‘গোপন নথি’ ভেবে আটকে রাখা এখনো তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অথচ নাগরিকের করের টাকা দিয়েই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, ফলে নাগরিকের কাছে তথ্য দেওয়া তাদের দায়িত্ব, দয়া নয়। এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন কাগজে-কলমে থাকলেও বাস্তব প্রয়োগে তা অনেকাংশে ভঙ্গুর। গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও স্বচ্ছ শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্য প্রবাহ অপরিহার্য হলেও এখনো সেই সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি।

সরকারি কর্তাদের মনোভাব
আমাদের প্রশাসনিক কাঠামোয় তথ্য প্রকাশকে এখনো ‘ঝুঁকি’ কিংবা ‘বিপদ’ হিসেবেই দেখা হয়। অনেক কর্মকর্তা মনে করেন, তথ্য উন্মুক্ত হলে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে, ভুল-ত্রুটি ধরা পড়বে কিংবা তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু হবে। এই ভয়ে তারা তথ্য গোপন রাখাকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে দেখেন। এখানে আরেকটি দিকও আছে, আমলাতন্ত্রের দীর্ঘদিনের সংস্কৃতি। সরকারি দপ্তরের পরিবেশ এখনো গোপনীয়তার চর্চায় অভ্যস্ত। ‘ফাইল বাইরে যাবে না’, ‘নথি দেখা যাবে না’, ‘উচ্চ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কিছু বলা যাবে না’—এসব নীতির মধ্যে বড় হয়ে উঠেছেন আমাদের অধিকাংশ কর্মকর্তা। ফলে নাগরিক তথ্য চাইলে স্বাভাবিকভাবেই বিরক্তি বা প্রতিরোধের মনোভাব তৈরি হয়। নাগরিক যেন অধিকার প্রয়োগ করতে এসে ‘অপরাধী’ হয়ে যান। আসলে এই মনোভাব এক ধরনের ভ্রান্ত ধারণা থেকে এসেছে।
কর্মকর্তারা ভাবেন, তথ্য প্রকাশ মানে দায় বাড়ানো, সমালোচনার মুখে পড়া। অথচ প্রকৃতপক্ষে তথ্য প্রকাশ কর্মকর্তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এতে তাদের কাজের স্বচ্ছতা প্রমাণিত হয়, জবাবদিহি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ থেকেও তারা মুক্ত থাকতে পারেন। তথ্য গোপন রাখা মানে শুধু নাগরিককে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা নয়, বরং কর্মকর্তা নিজেকেও অযাচিত সন্দেহের মুখে ফেলে দেওয়া। আজকের দিনে যেখানে ডিজিটাল প্রযুক্তি, ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তথ্য লুকানো প্রায় অসম্ভব—সেখানে গোপনীয়তার সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে থাকার মানে হলো জনগণের সঙ্গে আস্থার সম্পর্ককে নষ্ট করা। ফলে সরকারি কর্তাদের উচিত হবে তথ্য প্রকাশকে ‘বাধ্যবাধকতা’ নয়, বরং ‘অর্জন’ হিসেবে দেখা। নাগরিককে সঠিক তথ্য দেওয়ার মাধ্যমে কর্মকর্তারা যেমন নিজেদের কাজের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারেন, তেমনি রাষ্ট্রীয় সেবার মানকেও উন্নত করতে পারেন।
আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট
তথ্য অধিকার শুধু উন্নত বিশ্বের বিলাসিতা নয়; বরং এটি এখন একটি বৈশ্বিক গণতান্ত্রিক মানদণ্ড। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোতেও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ভারত, নেপাল কিংবা শ্রীলঙ্কায় তথ্য অধিকার আইন শুধু কাগজে-কলমে নেই; বাস্তবে এর প্রয়োগও তুলনামূলকভাবে দৃশ্যমান। বিশেষ করে ভারতে তথ্য অধিকার আন্দোলন সামাজিক পরিবর্তনের বড় হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। হাজার হাজার দুর্নীতির ঘটনা উন্মোচিত হয়েছে, সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে, এমনকি জনস্বার্থে নীতিমালার পরিবর্তন ঘটেছে। আবার আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশেও তথ্য অধিকার আইন জনগণের জীবনমান উন্নয়নে ব্যবহার হচ্ছে। সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্যপ্রবাহকে কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে দেখা হয়। উন্নত দেশগুলোর উদাহরণ আরও শক্তিশালী। ইউরোপ কিংবা উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ দেশে বাজেট, টেন্ডার, সরকারি চুক্তি, প্রকল্পের অগ্রগতি—এসব তথ্য নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত। ওয়েবসাইটে কয়েকটি ক্লিক করলেই যে কেউ এসব তথ্য পেয়ে যায়। আলাদা করে আবেদন করার প্রয়োজন পড়ে না। ফলে স্বচ্ছতা ও আস্থার পরিবেশ স্বাভাবিকভাবে তৈরি হয়।
বাংলাদেশের জন্যও এই ধারা অনুসরণ করা জরুরি। কারণ, আইন প্রণয়ন করা হলেও প্রয়োগের কাঠামো দুর্বল হলে তার সুফল নাগরিকেরা পাবে না। বরং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের উচিত হবে সরকারি তথ্য ব্যবস্থাপনাকে ধীরে ধীরে ডিজিটাল ও নাগরিক-বান্ধব করে তোলা। তথ্য গোপনের সংস্কৃতি যত কমবে, গণতন্ত্র তত বেশি শক্তিশালী হবে।
তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রয়োজন কার্যকর পদক্ষেপ
আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস কেবল একটি আনুষ্ঠানিক দিন নয়, বরং এটি আমাদের সামনে নতুনভাবে করণীয় তুলে ধরে। বাংলাদেশে আইন আছে, কিন্তু কার্যকারিতা বাড়াতে হলে কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি—
প্রাক-প্রকাশ নীতি (Proactive Disclosure): তথ্য অধিকার আইনের সবচেয়ে কার্যকর ধাপ হতে পারে প্রাক-প্রকাশ নীতি। সরকারি বাজেট, খরচের হিসাব, উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি, টেন্ডার প্রক্রিয়া, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ—এসব তথ্য ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে। এতে নাগরিকের আবেদন কমবে, স্বচ্ছতাও বাড়বে।
প্রশিক্ষণ: প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বড় একটি অংশ এখনো তথ্য অধিকার আইনের ধারা সম্পর্কে অবহিত নন। প্রতিটি তথ্য কর্মকর্তা ও সরকারি কর্মকর্তাকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে—তথ্য দেওয়া মানে আইন মানা, দায় বাড়ানো নয়।
জনসচেতনতা: শুধু আইন জানলেই হবে না; মানুষকেও জানতে হবে তাদের অধিকার। গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত প্রচারণা চালাতে হবে—’তথ্য চাওয়া অপরাধ নয়, অধিকার।’ সাধারণ মানুষ যদি সচেতন হয়, তাহলে প্রয়োগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাড়বে।
ডিজিটাল ব্যবস্থা: তথ্য সরবরাহের প্রক্রিয়া যত বেশি ডিজিটাল হবে, তত কমবে হয়রানি ও গোপনীয়তার সুযোগ। অনলাইনে আবেদন ও সরবরাহের ব্যবস্থা করলে নাগরিক সহজে তথ্য পাবে, আর কর্মকর্তাদেরও কাজ সহজ হবে।
তথ্য কমিশনের শক্তি বৃদ্ধি: তথ্য কমিশন বর্তমানে জনবল, অর্থ ও ক্ষমতার ঘাটতিতে ভুগছে। কমিশনকে শক্তিশালী না করলে আইন কেবল কাগজেই থাকবে। কমিশনের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা, স্বাধীনতা ও প্রযুক্তিগত সুবিধা দিতে হবে, যাতে তারা কার্যকরভাবে আইন বাস্তবায়ন করতে পারে।
সারকথা হলো, তথ্য অধিকার আইন শুধু কাগজে থাকলে চলবে না; এটিকে জীবন্ত করতে হলে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রশাসনিক সংস্কৃতি পরিবর্তন, জনসচেতনতা এবং প্রযুক্তির সমন্বয় প্রয়োজন।
তথ্যই শক্তি, নাগরিকই স্বত্তা
তথ্য অধিকার দিবস কেবল কাগুজে উদযাপন নয়, বরং নাগরিকদের জানার অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার। আমরা যদি সত্যিকারের উন্নত, গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র চাই, তবে তথ্য প্রবাহকে সহজ করতে হবে। ‘তথ্য চাইলে সরকারি কর্তাদের হয় মাথা নষ্ট’—এই প্রবণতা বদলাতে হবে। বরং আমাদের সংস্কৃতি হতে হবে তথ্য চাওয়া মানে স্বাভাবিক বিষয়, তথ্য দেওয়া মানে দায়িত্ব পালন।
তথ্যের আলো ছাড়া গণতন্ত্রের অন্ধকার দূর করা সম্ভব নয়। তাই তথ্য অধিকার আইনকে শক্তিশালী করে বাস্তবে প্রয়োগ করা, সরকারি কর্মকর্তাদের মনোভাব পরিবর্তন করা এবং নাগরিকদের সচেতন করে তোলা—এই তিন দিকেই মনোযোগ দিতে হবে। কারণ, তথ্য মানেই শক্তি; আর এই শক্তি নাগরিকের কাছেই ফিরিয়ে দেওয়াই হলো প্রকৃত গণতন্ত্রের বিজয়।